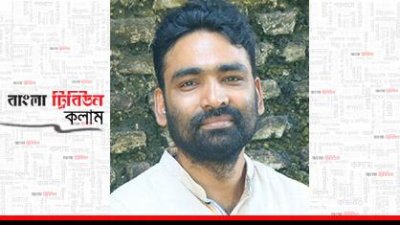শিরোনাম দেখে চমকে উঠবে না। মুক্ত গণমাধ্যমের ধারণাকে ত্রুটিপূর্ণ বলছি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। তার অর্থ কি এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উন্নত ইউরোপের দেশ, বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো এবং পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে পরিচিত ভারতেও মুক্ত গণমাধ্যমের ধারণাটি ত্রুটিমুক্ত? এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত ‘না’।
কেননা, গণমাধ্যম কখনও মুক্ত হয় না। মুক্ত হতে পারে না। তবে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তার ভেতরে থাকে। অন্যের মুক্তির জন্য লড়াই-সংগ্রাম করে করে ক্লান্ত গণমাধ্যমের নিজের মুক্তির প্রসঙ্গটি অনেক সময় প্রসঙ্গের বাইরে থাকলেও প্রতি বছরের ৩ মে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সেই আলোকে এই সময়ের বাংলাদেশে মুক্ত গণমাধ্যমের তর্কটি কেমন হওয়া উচিত— সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।
গণমাধ্যম আসলে কী করে? সে মানুষকে তথ্য দেয়, বিনোদন দেয়, শিক্ষা দেয় বা শিক্ষার পথ বলে দেয় ইত্যাদি। গণমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য হলো, সকল সংবাদমাধ্যমই গণমাধ্যম, কিন্তু সকল গণমাধ্যমই সংবাদমাধ্যম নয়। যেমন, একটা সিনেমার চ্যানেল বা কার্টুন অথবা খেলার চ্যানেলকে গণমাধ্যম বলা যাবে, কিন্তু যতক্ষণ না সে সংবাদ প্রচার করছে, ততক্ষণ সে সংবাদমাধ্যম নয়। সে কারণে সংবাদমাধ্যমের দায় ও দায়িত্ব গণমাধ্যমের চেয়ে বেশি। আর সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে বলা হয়, তার প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা কমানো। কিন্তু মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা কমানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কিংবা দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মানুষদেরই প্রতিনিয়ত নানাবিধ অনিশ্চয়তার ভেতরে থাকতে হয়। তাকে প্রতিনিয়ত ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়।
ফলে ক্ষমতাকাঠামো চায় গণমাধ্যমকে শৃঙ্খলিত করে রাখতে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সফলও হয়।
গণমাধ্যম বস্তুত সব আমলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শৃঙ্খলিত থাকে। অর্থাৎ গণমাধ্যম কখনই মুক্ত বিহঙ্গ নয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পাখি ও ঘুড়ির মতো। চিড়িয়াখানায় বা খাঁচাবন্দি নয় এমন পাখিরা ওড়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন। ঘুড়িও আকাশে ওড়ে। পাখি যতটা উপরে ওঠে অনেক সময় ঘুড়ি তারও চেয়ে বেশি উপরে যায়। কিন্তু ওড়ার ক্ষেত্রে ঘুড়ির স্বাধীনতা ততটুকু, নাটাই ধরে রাখা ব্যক্তিটি যতটুকু সূতা ছাড়বেন। গণমাধ্যমের নাটাইও নানাজনের হাতে ধরা থাকে। তারা তাদের সুবিধামতো সূতা ছাড়েন। গণমাধ্যম স্বাধীন। কিন্তু তার নাটাই ধরা থাকে রাষ্ট্রীয় বিবিধ আইন, কানুন, নীতিমালা এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর বিধিবর্হ্ভিূত আচরণের হাতে।
কার সংবাদ প্রচার করা যাবে বা যাবে না; কোন সংবাদের ট্রিটমেন্ট কেমন হবে; কোন সংবাদটি ‘কিল’ (ব্ল্যাকআউট) করতে হবে; কোন ব্যক্তিকে টকশোতে আনা যাবে না ইত্যাদি নানাবিধ প্রেসক্রিপশন মেনে চলতে হয় গণমাধ্যম পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের।
অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে সেই পরিস্থিতির কি খুব বেশি উন্নতি হয়েছে? আগে যাদের সংবাদ প্রচার করা যেত না, এখন তাদের সংবাদ সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয় বা প্রচার করতে হয়। সেজন্য সরকারের তরফে হয়তো বড় কোনও চাপ নেই। কিন্তু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো স্বপ্রণোদিত হয়েই এটা করে। এটা যতটা না বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে, তার চেয়ে বেশি অতীতের ‘কাফফারা’। অনেকে অতি উৎসাহ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ দল ও ব্যক্তির অনুকম্পা প্রার্থনা করেন।
রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী, বিশেষ করে গোয়েন্দা বাহিনীর তরফে নিউজরুমে ফোন করে শাসানো বা পরামর্শের মোড়কে নানাবিধ এজেন্ডা বাস্তবায়নের নির্দেশ ও নির্দেশনার পরিমাণ হয়তো কমেছে কিংবা হয়তো এই জাতীয় নির্দেশনা এখন আসে না— কিন্তু তার বিপরীতে তৈরি হয়েছে মবের ভয়।
গত বছরের ৫ আগস্টের পরে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, এখন ফেসবুকে কেউ একটা কর্মসূচি ঘোষণা করলেই দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানটিও ভয় পেয়ে যায় এবং তার নিরাপত্তার জন্য অফিসের নিচে শুধু পুলিশ না, সেনাবাহিনীও মোতায়েন করতে হয়! যারা ভয় দেখাচ্ছেন তারা হয়তো নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীও নন। কিন্তু তারা রাজনৈতিক দলের চেয়েও ক্ষমতাবান। কখনও মনে হতে পারে তারা বুঝি রাষ্ট্রের চেয়েও বেশি ক্ষমতাধর। সম্প্রতি তিনটি বেসরকারি টেলিভিশনের চার জন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে শুধুমাত্র ফেসবুকের একটি পেইজে হুমকি দেওয়ার কারণে। সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় যদিও বলেছে যে, ওই সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুতি পেছনে তাদের কোনও হাত নেই। কিন্তু যাদের হাত আছে, তাদের হাত সরকারের চেয়েও বড় কিনা, এই প্রশ্নও জনমনে আছে।
২.
আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে মুক্ত গণমাধ্যম বা Free Press-এর ধারণাটি সামনে এসেছে। এর শেকড় রয়েছে ১৭ ও ১৮শ শতাব্দীর ইউরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে যখন রাষ্ট্রীয় বা রাজকীয় সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীন মত প্রকাশের দাবি সামনে নিয়ে আসতে শুরু করেন।
জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্য পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে নাগরিকের বাকস্বাধীনতার পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তার বিপরীতে এমন সব আইনি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে যে, গণমাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার নাটাই তুলে দেওয়া হয়েছে ওইসব আইন, বিধি-বিধান, রাষ্ট্রীয় বাহিনী তথা ক্ষমতাবানদের কাছে। এই ক্ষমতা কখনও রাজনৈতিক, কখনও সামাজিক, কখনও রাষ্ট্রীয়, কখনও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজেই, কখনও বিজ্ঞাপনদাতা গোষ্ঠী, কখনও অরাজনৈতিক কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী—যারা শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় কর্মসূচি ঘোষণা করেই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ভীত নাড়িয়ে দিতে পারে— সাম্প্রতিক সময়ে যে প্রবণতাটি সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। এরকম বাস্তবতায় মুক্ত গণমাধ্যম বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার আলাপ অনেকটা আম গাছের কাছে কাঁঠাল চাওয়ার মতো।
৩.
মুক্ত গণমাধ্যম বলতে আপনি আসলে কী বোঝেন?
ক. রাষ্ট্র বা করপোরেট চাপমুক্ত সংবাদ পরিবেশন।
খ. সাংবাদিকের পেশাগত নিশ্চয়তা।
গ. সত্য যাচাই ও জনস্বার্থে রিপোর্টিং।
ঘ. সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারের পরে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা।
ঙ. জেনেবুঝে তথ্যের নামে অপতথ্য প্রকাশ না করা।
চ. ভুল হলে স্বীকার করে নেওয়া।
এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের সুযোগ কম যে, বাংলাদেশে মুক্ত গণমাধ্যম বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় হলো সাংবাদিকের পেশাগত অনিশ্চয়তা। যে মানুষটি জানেন না আগামী মাসে তার বেতন কবে হবে বা তিনি তার পাওনাটুকু কবে বুঝে পাবেন; যে মানুষটি জানেন না আগামী মাসে তার চাকরিটা থাকবে কিনা এবং চাকরি চলে গেলে তিনি তার পরের মাসে আরেকটা চাকরি পাবেন কিনা, তার কাছে আপনি যখন সাহসী, বস্তুনিষ্ঠ, নির্মোহ ও স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রত্যাশা করেন কোন আক্কেলে?
সে কারণেই বলেছি বাংলাদেশে মুক্ত গণমাধ্যমের ধারণাটিই ত্রুটিপূর্ণ। মুক্ত গণমাধ্যম পেতে চাইলে আগে সাংবাদিকের চাকরির নিশ্চয়তা দিতে হবে। রাষ্ট্রকে সেরকম একটি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এখন পর্যন্ত সংবাদপত্রের সাংবাদিকের জন্য ওয়েজবোর্ড বা বেতন কাঠামোটিই ঠিকমতো মানানো যায়নি। উপরন্তু টেলিভিশন এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যমের জন্য ওয়েজবোর্ড বলে কোনও শব্দই নেই।
৪.
মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্র ও রাজনীতি কখনই গণমাধ্যমবান্ধব হয় না। ক্ষমতাবানরা সব সময়ই চায় তাকে চাপে রাখতে। ক্ষমতাবানরা চায় গণমাধ্যম শুধু তার প্রশংসা করবে। তার খারাপ ও অন্ধকার দিকগুলো আড়াল করে শুধু তার ভালো দিকগুলো তুলে ধরবে।
ফলে নানা সংকট ও চাপের মধ্যেও গণমাধ্যম সেই কাজ কতটুকু করতে পারছে—সেটি বিরাট প্রশ্ন। গণমাধ্যম এই চাপ ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে নিজের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে কি না—সেটিই বিবেচ্য। বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশ কোথায় থাকলো এই প্রশ্নের চেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের সাংবাদিক, গণমাধ্যমকর্মীরা নিজেদের সংকটগুলো সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল এবং তারা আত্মসমালোচনা করতে পারছেন কিনা।
পরিশেষে, মুক্ত গণমাধ্যম শুধু মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নয়, এটি একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্য ও জবাবদিহিরও মাপকাঠি। সুতরাং যারা সেই জবাবদিহি নিশ্চিতে কাজ করবেন, তাদের জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত রেখে মুক্ত গণমাধ্যমের আলোচনা নিরর্থক।
লেখক: সাংবাদিক