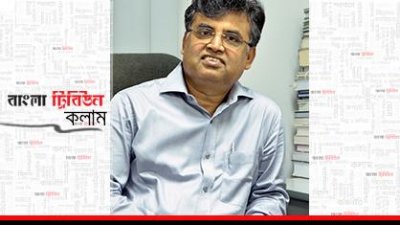বাঙালি জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী অবস্থানে আছে এ কথা এই মুহূর্তে বললে অসত্য বলা হবে। বরং চরম সত্য হলো, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এখন অন্তিম দশায়। এমনকি এভাবেও যদি বলা হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ অন্তর্জলী যাত্রায় অবস্থান করছে– অর্থাৎ মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষমাণ, যেকোনও মুহূর্তে মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে যাবে। বাঁচবার কোনও শক্তি তার নেই। এ সত্য কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে? না তাও একেবারে সম্ভব নয়।
বাঙালি জাতীয়তাবাদের কেন এ অবস্থা হলো? বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই অন্তিম দশার জন্যে কোনও একজন বা কোনও একটি রাজনৈতিক দল বা কোনও একটি প্রজন্মকে দায়ী করার সুযোগ নেই। বরং সুদূর অতীত, নিকট অতীত ও বর্তমানে দাঁড়িয়ে প্রথমে বিচার করা দরকার, বাঙালি জাতীয়তাবাদের আসলে কি কোনও অন্তর্নিহিত শক্তি হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি হয়েছিল? হাজার হাজার বছর ধরে বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য জন্মেছিল নানান রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাত্যভিমান বা জাতিগত চেতনার জন্ম কতখানি হয়েছিল? বলা যেতে পারে সে সময়ে এই আধুনিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়নি। তবে এটা তো ঠিক, ওই হাজার হাজার বছরে বাঙালি তো নানান সময়ে নানানভাবে বিদেশি শাসকের অধীনে শাসিত হয়েছে। ওই সব শাসনকালে নিষ্পেষিত হওয়ার ফলে বাঙালির মধ্যে একটা জাতিগত চেতনা জেগেছে এমন কোনও উদাহরণ তো মেলে না।
রাজপুতদের অনেকেই মোগলদের সহায়তা করেছে। মানসিং’র তরবারিতে আকবরের রাজত্ব বেড়েছে। যশোবন্ত সিং’র তরবারিতে আওরঙ্গজেবের রাজত্ব বেড়েছে। কিন্তু তারপরেও রাজপুত রানাদের নেতৃত্বে শত শত বছর ধরে একটা সংগ্রাম ও প্রতিবাদের জীবনের ভেতর দিয়ে অধিকাংশ রাজপুতের যেমন একটা রাজপুত জাতীয়তাবাদ না হোক রাজপুত পরিচিতির প্রতি গর্ব জন্মেছিল, বাঙালির কিন্তু সেন, পাল থেকে শুরু করে খিলজি বা মোগল আমল অবধি বিদেশিদের দ্বারা শাসিত হয়েও ওই ধরনের কোনও বাঙালি পরিচয় নিয়ে গর্বের ইতিহাস বা বাঙালির দেশ বা রাজ্য চেতনা দেখা যায় না। অমন সংগ্রামও দেখা যায় না। মোগলদের বিরুদ্ধে বারও ভূঁইয়ারা লড়েছে– কিন্তু সেখানে কোনও ভূখণ্ড কেন্দ্রিক জাতি চেতনার উন্মেষ ছিল না। যার ফলে মোগল আমলের শেষে এসে মোগলদের থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসে নিজস্ব রাজত্ব কায়েম করা আলীবর্দীর নাতি সিরাজের যখন ইংরেজের হাতে পতন হয়, সে সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও জাতিগত বা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল না। বরং ইতিহাসে মেলে নবাবের পতনের ও নতুন নবাবের রাজ্য গ্রহণের খবর শুনে সাধারণ গ্রামের মানুষ সেদিন জানতে চেয়েছিল, এবার ধানের দাম বাড়বে কিনা? এই বাস্তবতাকে ঢেকে রেখে, পরবর্তীতে কয়েক যাত্রা পালাকার ও কিছু ঐতিহাসিক নানান কল্পনা জুড়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করতে নতুন মূর্তি গড়েছিলেন। কিন্তু আর যাই হোক সে মূর্তি যেমন বাস্তবে সত্য নয়, তেমনই তার ভেতর মানুষের দেশ চেতনা বা জাতীয়তাবাদের কোনও চেতনা ছিল না।
তাই সত্যি অর্থে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়– যার সব উপাদান বাঙালির সংস্কৃতিতে ও মাটিতে আছে– এ নিয়ে বাঙালি সজাগ হয়েছে বা এই জাতীয়তাবাদকে খুঁজেছে অনেক পরে। ব্রিটিশ আসার পরে বাঙালির ধীরে ধীরে যে নবজাগরণ হয়েছে তারও শুরুতে কিন্তু বাঙালির জাতীয়তাবাদ বা দেশকে খোঁজা হয়নি। বাঙালির নবজাগরণের অগ্রপথিক রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায়কে একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তিনি সত্য বুঝেছিলেন, তাঁর সময়টা আর যাই হোক ভারতবর্ষ বা বাঙালির স্বাধীনতা চাওয়ার সময় নয়। কারণ, দেশ ও মানুষ প্রস্তুত নয়। বরং তার মূল কাজ হলো ভারতবাসীর হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজ যে অন্ধত্বের মধ্যে পড়ে আছে সেখান থেকে তাদের বের করে আনা। তিনি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, তুর্কি, মোগল, আফগান, প্রভৃতি আক্রমণকালে ভারতবর্ষের নালন্দা, তক্ষশীলাসহ সব বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে একটা দীর্ঘ সময় ভারতবর্ষ জ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। ভারতবর্ষের জ্ঞানচর্চা টোল ও মক্তবে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে শুধু সমাজে নানান ধরনের অন্ধত্ব শুধু আসেনি সঙ্গে সঙ্গে সকল মাদার নলেজের বই তাই সে ভারতীয় সিভিলাইজেশানের হোক আর সেমেটিক সিভিলাইজেশানের হোক– সব কিছুই টোলের পণ্ডিত আর মক্তবের কম শিক্ষিত বা অনেকখানি অন্ধ শিক্ষকদের দ্বারা ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। রামমোহনের চেষ্টা তাই ছিল ভারতীয় সিভিলাইজেশানের বেদ, উপনিষদ, ন্যায়শাস্ত্র, গীতা এমনি সকল বই যা ধর্মীয় বই নামে ততদিনে চিহ্নিত হয়ে গেছে অন্যদিকে সেমেটিক সিভিলাইজেশনের সকল মাদার নলেজ বা ধর্মীয় বই নামে পরিচিত বই তার প্রকৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা।
এছাড়া দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার ফলে জ্ঞানের উপকরণ বইয়ের যে প্রচলন ঘটেনি সেই ছাপা বইয়ের প্রচলন ঘটানো। যাতে জ্ঞান সকলের কাছে পৌঁছায়। তাই তাঁর আন্দোলন ছিল মূলত মানুষের অন্ধত্ব ঘোচানোর আন্দোলন। সেখানে জাতীয়তাবাদের কোনও ইঙ্গিত দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, তা ভারতবাসী বলে উল্লেখ বাঙালি জাতীয়তাবাদ নয়। তাই রামমোহনকে ঘিরে বা তার অনুসারীদের আন্দোলনে দেশ বা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এমন কোনও ইঙ্গিত মেলে না। বরং সেখানে সমাজের অন্ধত্ব ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টাই দেখা যায়। সত্যি অর্থে দেশ ‘মা’ বা ‘দেশমাতা’ এই ধারণা আসে মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা থেকে। মাইকেল, রেখ মা দাসেরে মনে- বলে দেশকে মা বলে ডাকেন। কিন্তু তখনও তাঁর সে ডাক কোনও তরঙ্গ এ সমাজে তোলেনি। তাই সত্যি অর্থে বাঙালি সমাজে ও এমনকি ভারতবর্ষে দেশকে মা বলে ডাকায় উদ্বুদ্ধ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘বন্দেমাতরম’ কবিতার মাধ্যমে। আর এই দেশকে মাতৃজ্ঞানে সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে একটা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। কিন্তু সেখানে শুরুতেই কিছু বৈপরীত্য ঘটে যায়, যা জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তার ‘বন্দেমাতরম’ কবিতাটি আগে লিখলেও পরে তা ব্যবহার করেন তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে। সেখানে তিনি দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে যে শ্রেণিটি তৈরি করেছেন, তারা সংসার ত্যাগী অর্থাৎ ধর্মীয় সন্ন্যাসী। অর্থাৎ দেশ ও মানুষের মুক্তির জন্যে, দেশকে মা বলে ডেকে জাতীয়তাবাদের পৌঁছানোর জন্যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম ও মানুষের মধ্যে তিনি সরাসরি সংযোগ ঘটালেন না। তিনি তাঁর মধ্যে অনুঘটক হিসেবে ধর্মকে দিয়ে দিলেন। আর এরই প্রতিফলন দেখা গেলো বাংলার ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিযুগের স্রষ্টা অরবিন্দ ঘোষের (ঋষি অরবিন্দ নামে পরে বেশি পরিচিত) মধ্যেও। তিনিও সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে ব্রিটিশকে ভীত করে তোলার জন্যে যে বিপ্লবী আন্দোলনের শুরু করলেন, সেখানেও তিনি বিপ্লবী হওয়ার জন্যে শুধু রাষ্ট্রীয় চেতনা বা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন না। এই রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম ও জাতীয় চেতনার কাছে নিয়ে আসার জন্যে তিনিও মাঝখানে অনুঘটক হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করলেন। সেখানে বাঙালি হিন্দুর প্রাকৃতজনের শক্তির দেবতা বলে কথিত কালীকে শক্তি ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়ার অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করা হলো। অর্থাৎ সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম শুরু হলেও সেখানে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্ম থেকে গেলো। অরবিন্দর এই পথকে আরও নগ্নভাবে পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগের রাজনীতি শুরু থেকে ধর্ম ভিত্তিক। যে কারণে তারা একটু কোণঠাসা ছিল। তবে মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় হলেও তার উৎপত্তি বেঙ্গলে হওয়ায়, বাংলায় তার আধিপত্য একটু বেশি ছিল। তবে মুসলিম লীগের জন্মের এক বছর আগে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সে সময়ের বৃহৎ বঙ্গ প্রদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিলে কলকাতা কেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণি হিন্দুও মুসলমান বঙ্গভঙ্গ রোধের একটা আন্দোলন শুরু করেন। অন্যদিকে, পূর্ববঙ্গ কেন্দ্রিক একটি শিক্ষিত ও ধনী মুসলিম শ্রেণি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। কারা সঠিক ছিলেন কারা ভুল করেছিলেন সে বিতর্ক এখানে নয়। তবে কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে যে একটা বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এর ভেতর খুব ক্ষীণকায়া একটি স্রোতের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি স্রোতরেখা ক্ষণিকের জন্যে কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের খুব অল্প একটি অংশের ভেতর দেখা গিয়েছিল। যা একেবারে সমাজের ওপর তলায় ছিল।
ওই কলকাতারও নিচের তলার মানুষ জানতো না বাস্তবে কী ঘটছে? সাধারণ মানুষ যে সে সম্পর্কে কিছুই জানতো না তার প্রমাণ মেলে ওই সময়ে নিয়ে লেখা গজেন্দ্র কুমার মিত্রের ‘কোলকাতার কাছে’ উপন্যাসের এক চরিত্রর বক্তব্যে। বক্তব্য এমনই ছিল, শহরে কী ঘটছে? ঠাকুরবাড়ির ছেলেটাও খালিপায়ে রাজপথে এসেছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গভঙ্গ রোধ বা বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে ওই সময়ে রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্য কবিরা যেসব গান লিখছেন তার কিছুই পৌঁছায়নি। তারা শুধু দেখেছিল ঠাকুরবাড়ির এই দেবতার মতো দেখতে ছেলেটি খালি পায়ে রাজপথে এসেছে। বাস্তবতা হলো সে ছেলেটিও শেষ অবধি ওই আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান। আর সত্যি অর্থে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে আর ওই অর্থে রাজনীতির দিকে আর মুখ ফেরাননি। বরং বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে সরাসরি রাজনীতিবিদদের সঙ্গে এসে তিনি তাদের মুখোশের আড়ালের প্রকৃত মুখটি দেখতে পান। সে মুখের ভেতর তিনি দেশপ্রেমও দেখেননি, জাতীয়তাবাদও দেখেননি। বরং দেখেছিলেন– ক্ষমতা, লোভ, স্বার্থপরতাসহ অনেক নিচুমানের কিছু। তাই বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের মাঝখানে রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার পরে জীবনের অনেকটা শেষ প্রান্তে এসে তিনি একবার মাত্র রাজনীতির দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তা শুধু সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্যে। মহাত্মা গান্ধী যখন চরম নিচুতায় নেমে সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি পদ কেড়ে নিলেন সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রতিবাদ করেননি, সুভাষ বসুকে দেশনায়কের পদে বরণ করেন আশীর্বাণী পাঠিয়ে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু বাঙালি নেতা হলেও তিনি সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসী ও তারই প্রতীক ছিলেন। তাই তাঁর আন্দোলনের ও রাজনীতির মধ্য দিয়ে কোনও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেনি।
তবে গান্ধী ভারতীয় রাজনীতি থেকে সুভাষ বসুকে এক প্রকার বিদায় করে দিতে সমর্থ হওয়ার ফলে দুটো ঘটনা শক্তভাবে ঘটে। এক, কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধী ধর্মকে বেশ শক্তভাবে নিয়ে আসেন। যার ফলে গান্ধী ভারতের হিন্দু সমাজের আরেকটি ‘অবতার’ হলেন কিন্তু ওই অর্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কোনও নেতা তিনি হলেন না। তবে তাঁর এই হিন্দুত্ব’র শক্ত অবস্থান বাংলার রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ গান্ধী যখন কংগ্রেসকে হিন্দুত্ব’র পথে নিয়ে গেলেন তখন তার বিপরীত ক্রিয়া হিসেবে মুসলিম লীগ রাজনীতিতে বৈধতা পেলো আগের থেকে বেশি। আর মুসলিম লীগের উৎপত্তি যেহেতু পূর্ব বাংলায়, তাই পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের ভিত্তি দৃঢ় হলো। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক যদিও পূর্ব বাংলায় রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের যোগ না ঘটিয়ে কৃষকের দুর্দশা অর্থাৎ অর্থনৈতিক কর্মসূচির যোগ ঘটিয়ে রাজনীতি ও মানুষের মধ্যে একটা সংযোগ সৃষ্টি করেছিলেন– সেটাও তিনি ধরে রাখতে পারেননি। কারণ, কংগ্রেস সেদিন ধর্মের বিচারে দেখেছিল শেরেবাংলাকে। তবে এর পাশাপাশি এও সত্য, শেরেবাংলার রাজনীতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কখনোই ছিল না। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির আগে সর্বশেষ খুব ক্ষীণ আকারে মুসলিম লীগের ও কংগ্রেসের কয়েক নেতা আলাদা বাংলাদেশ গড়ার একটা চেষ্টা করেছিলেন– সেখানে শরৎ বোস ছাড়া কংগ্রেসের অন্য হিন্দু নেতারা যেমন আসেননি, হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি যেমন আসেননি, তেমনি শেরেবাংলাও যাননি। শেষ অবধি বাঙালি জনগোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমান নামে ভাগ হয়ে গেলো বাংলা ভাগের মধ্য দিয়ে। তাই রামমোহনের আমল থেকে ৪৭ এর দেশভাগ অবধি খুঁজলে কিন্তু ওই অর্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্ষীণকায় স্রোতরেখা ছাড়া কোনও ছোট খাট নদীর দেখাও মেলে না।
এরপরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক চিলতে আলোর রেখা বলে ধরা হয় পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর পরই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে। এই ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিকগুরু ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ যদিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ যুক্তিতে বাংলা ভাষার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, এবং তাঁর সঙ্গে অনেকেই সেদিন এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকলকে মূলত যে কাজটি করতে হয়েছিল তা হলো পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের শাসক চক্রের কাছে যুক্তি সহকারে এই সত্য তুলে ধরা– বাংলা কোনও অর্থেই শুধু হিন্দু বাঙালির ভাষা নয়, এটা বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সকলেরই ভাষা। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ যেহেতু পূর্ববাংলার মুসলিমরা, অতএব তাদের ভাষাই রাষ্ট্রভাষা বা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হোক।
অর্থাৎ ভাষা যতই জাতীয়তাবাদের অন্যতম একটা উপাদান হোক না কেন, পূর্ব পাকিস্তানের শুরুতে ভাষা আন্দোলন কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের কারণে হয়নি। তবে যেহেতু ভাষা সব সময়ই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের একটি শক্ত উপাদান- তাই এই আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা সূক্ষ্ম আলোক রেখা সচেতন বা অবচেতনভাবে হোক পূর্ববঙ্গের অল্প সংখ্যক তরুণ বাঙালি মুসলিমের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। যে কারণে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের চিন্তার আরও একটু প্রসার ঘটে। আর এর কিছু আনুষ্ঠানিক অর্থাৎ যাকে আশ্রয় করে এই জাতীয়তাবাদ বিমূর্ত থেকে মূর্ত হতে পারবে তা সৃষ্টি হয় ষাটের দশক থেকে সনজিদা খাতুন, নওয়াজেশ আহমদ, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ কিছু সংখ্যক সংস্কৃতিকর্মীর হাত ধরে। যার ভেতর অন্যতম ছিল বাঙালির মাঠের পহেলা বৈশাখকে নান্দনিকরূপে রবীন্দ্র- নজরুলে সমৃদ্ধ করে নাগরিক জীবনে নিয়ে আসা। এ ধারায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে ষাটের দশক থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী গান, কবিতা, উপন্যাস ও ছায়াছবিও তৈরি হয় কিছু। কিন্তু অবিভক্ত বাংলায় যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক এই শিল্প সাহিত্যর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে বামপন্থী চিন্তা চেতনার শিল্প সাহিত্য এবং শিল্প সাহিত্যের সব শাখার একটি অংশকে জাতীয়তাবাদ থেকে শ্রেণি সংগ্রামে নিয়ে যায় তারা। এবং সেটা বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনেকখানি জায়গাও দখল করে নেয়।
এই একই ঘটনা ঘটে পূর্ব পাকিস্তানে ষাটের দশকে। যে কারণে বাঙালির রাষ্ট্রসৃষ্টির সংগ্রামে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণি-সংগ্রামের সমাজতন্ত্রকেও মেনে নিতে হয়। সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে এক স্রোতে প্রবাহিত করার কাজটি বাস্তবসম্মত না হলেও সেদিনের বাস্তবতায় তা করতে হয়েছিলো। অন্যদিকে যে ১৯৭০-এর নির্বাচনের ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের সৃষ্টি ওই নির্বাচনের প্রচারও কিন্তু শতভাগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে হয়নি। বরং সেখানে সব থেকে বেশি জোর পেয়েছিল পাকিস্তানের দুই প্রদেশের বৈষম্য। যতভাগ মানুষ এই বৈষম্যের অবসান চেয়েছিল ওই সংখ্যক মানুষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ধুদ্ধ হয়নি। যদিও স্বাধীনতার মূল অস্ত্র ছিল ‘জয় বাংলা’ স্লোগান। অন্যতম স্লোগান ছিল ‘তুমি কে,
আমি কে, বাঙালি, বাঙালি’– তারপরেও এই মূলঅস্ত্র ‘জয়বাংলা’ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে আর সকল বাঙালি মুখে নেয় না। এমনকি ১৯৭১-এও সব বাঙালি মুখে নেয়নি– এটাও বাস্তব সত্য।
তাই বাস্তব সত্য, বাঙালির বাংলাদেশ সৃষ্টিতে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তির চাহিদা যত বড় ভিত্তি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ তত বড় ভিত্তি ছিল না।
অন্যদিকে ১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রচারে অর্থনৈতিক ইস্যু, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য, জাতীয়তাবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও রাজনীতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ ঘটাতে অরবিন্দু ঘোষ, গান্ধীর মতো ধর্মকে অতখানি অনুঘটক না রাখলেও ধর্মকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়নি। সেখানে বলা হয়েছিলো, ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে রাষ্ট্র কোনও আইন প্রণয়ন করবে না। অর্থাৎ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি যেমন সমাজতন্ত্র আসে তেমনই ধর্মও থেকে যায় রাজনীতি ও রাষ্ট্রে। তাই স্বাধীনতার পরে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে এসে যায়। এমনকি সমাজের সব ধর্মের মানুষের চাহিদাও থেকে যায়– ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্র যেন একটা কর্তব্য পালন করে। অর্থাৎ বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি যেমন সমাজতন্ত্র থাকে তেমনি রাষ্ট্রে স্বীকৃত না হলেও ধর্ম অবস্থান করে নেয়। তাই পূর্ববাংলায় বাঙালির রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’ অনেক সংগ্রাম ও রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ একক ও শক্ত কোনও ভিত্তি পায়নি। তারপরেও বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েনে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আসা বাঙালির নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে বাস্তবে অস্থির সময় কাটাতে হয়। যার ফলে তাঁরা এমন কোনও সময় পাননি যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের গাছটিকে পরিপুষ্ট করবেন।
স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসা এই সরকারের অবসান হয় মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। আর তা সম্পূর্ণ হয় তাজউদ্দীন আহমদসহ জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় হত্যার মধ্য দিয়ে। এর পরে বাংলাদেশে সামরিক শাসকদের হাত ধরে যে রাজনীতি শুরু হয়, তারা এবং তাদের উত্তরসূরিরা কেউই রাজনীতি’র সঙ্গে মানুষের যোগ ঘটাতে ধর্মকে শুধু অনুঘটক রাখেননি। তারা সরাসরি মুসলিম লীগের মতো ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শুরু করে দেন। অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া দল আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও তার সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র এগুলো নিয়ে তাদের রাজনীতি বজায় রাখার ও মানুষকে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করে যেতে থাকে। কিন্তু তাদের এই পথ চলায় তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কাছে বড় ধাক্কা খায় ১৯৯১ সালের নির্বাচনে।
১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দিয়ে আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে যে রাজনীতি ছিল তাকে প্রতিহত করা হয়েছিল। ধর্মাশ্রয়ীরা সামরিক শক্তির মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সেদিন বিজয়ী হয়। কিন্তু ১৯৯১ সালে জনগণের ভোটের মধ্য দিয়ে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি জয়লাভ করে। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের ভেতর দিয়ে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির বিজয় মূলত ৫৪’র পরে এই ভূখণ্ডে নতুন করে ধর্মের রাজনীতির নির্বাচনি বিজয়। তাই রাজনীতির এই বিশাল পরিবর্তনের পরে আওয়ামী লীগও ধর্মের রাজনীতিকে প্রতিরোধ করার দীর্ঘ সংগ্রামে পা বাড়ায় না। বরং রাজনীতি ও মানুষের মধ্যে সংযোগ ঘটানোর জন্যে গান্ধী বা অরবিন্দর মতো ধর্মকে অনুঘটক হিসেবে নেয়। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে স্বাভাবিকভাবে ধর্মের জন্যে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিতে হয় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে। অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রোত রেখা আরও ক্ষীণ হয়।
তবে তারপরও নব্বই দশকের বা তার পরেও কিছুকালের সমাজে বাঙালির সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারাটি একেবারে জলশূন্য হয়নি। তাই ২০০৮-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয় লাভ করার ফলে তরুণ প্রজন্মের একটি শিক্ষিত অংশের মধ্যে একটা বাঙালিত্ব জেগে ওঠে। যা তার ভাষা ও সংস্কৃতি নির্ভর। যা তার মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত। যা তার ‘জয়বাংলা’ স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০১২-তে গণজাগরণ মঞ্চের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তবে সেটা ছিল আগুনের একটি ফুলকি মাত্র।
বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত শ্রেণিতে যতটুকু বাঙালি জাতীয়তাবাদ জেগেছিল বাস্তবে এ ছিল তার থেকেও কম বা তারই মতো এবং ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে এর বিপরীতে দ্রুতই ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় কলকাতা কেন্দ্রিক রবীন্দ্রনাথদের ওই বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের পাশে শেষ অবধি যেমন রাজনীতিবিদরা দাঁড়াননি। রাজনীতিবিদরা তাদের ক্ষমতার রাজনীতিতে চলে যান– এখানেও তাই ঘটে। গণজাগরণের আগুনের ফুলকিটি নিভিয়ে দিয়ে রাজনীতিকরা ক্ষমতার স্বার্থে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি ও অন্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনেক কিছুই মেনে নেন। যার ফলে ১৯৭৫ ও ১৯৯১-এর বিপর্যয়ের পরে ধর্মাশ্রয়ী বা ধর্মীয় অন্ধত্ব রাজনীতিতে ও রাষ্ট্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যতটা জায়গা দখল করতে সমর্থ হয় তার থেকে আরও বেশি জায়গা তারা ২০১২ থেকে ধীরে ধীরে দখল করছে। যে কারণে এখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি আনুষ্ঠানিক দিন ‘পহেলা বৈশাখ’ও সময়ের গণ্ডিতে বন্দি হয়ে পালিত হয়। এবং সময়ের স্রোতধারা এভাবে চলতে থাকলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যদি নিকট ভবিষ্যতে সময়ের গণ্ডির বদলে ফ্রেমে বন্দি একটি অতীতের ছবি হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।
তাই বলা যায় আসলে বাঙালির রাজনীতিতেও রাষ্ট্রচিন্তায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ খুব শক্ত অবস্থান কোনও সময়েই গড়ে তুলতে পারেনি। আর সময়ের ও রাজনীতির বিবর্তনে এখন অন্তিম দশায়।
কিন্তু এখানেই কি বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে? ভবিষ্যতে কি জাগবে না? বাস্তবে জাতীয়তাবাদের কখনোই পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে না। যেহেতু মানব সমাজ যেমন দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে তেমনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবে। মানব সমাজের এই পথ পাড়ি’র সংগ্রামই মূলত সংস্কৃতি। আর এর সঙ্গেই যুক্ত জাতীয়তাবাদ। তাই এর সমাপ্তি’র কোনও সুযোগ নেই। হাজার বছরের পথ চলায় সে গড়ে উঠবেই। আর এই পথ চলাতে মাঝে মাঝে মানব সমাজের ওপর যখন অন্ধকার নামে সে সময়ে চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের মতো ঢাকা পড়ে যায় জাতীয়তাবাদের মতো সংস্কৃতির অনেক উপাদান। যেকোনও জাতীয়তাবাদের মূলরস বা শেকড়ের রস থাকে তার নিজস্ব ভূখণ্ডের হাজার বছরের সংস্কৃতিতে। এই সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের শক্তি বাস্তবে ধর্মভিত্তিক কোনও বিষয়ের থেকে এমনকি ভাষাভিত্তিক কোনও বিষয়ের থেকেও অনেক বেশি। কারণ, সংস্কৃতি নির্ভর সবকিছুই সব সময় নমনীয় ও উদার। যার সবটুকু মানুষের জীবনের সব ধরনের সত্য সংগ্রাম দিয়ে গঠিত। আর এ কারণে সব সংস্কৃতির সারটুকু সুন্দর। আর সুন্দরের মিলনই সংস্কৃতি নির্ভর জাতীয়তাবাদের চরম প্রকাশ ঘটায় মানববাদের মধ্য দিয়ে। আর ওই লক্ষ্যই যেকোনও জাতিগোষ্ঠী বা মানবগোষ্ঠীর প্রকৃত গন্তব্য। আর মানুষ বিজয়ী হতেই জন্মেছে। তাই যে কোনও অন্ধকারকে ঠেলে সে তার বিজয়ের দিকে এগিয়ে যায়।
মানুষের এই বিজয়ের পথের বিপরীতে মানুষের সমাজে মাঝে মাঝেই কট্টরপন্থা জয়লাভ করে ঠিকই। তবে অন্ধের জয়লাভ, কঠোরতার জয়লাভ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। শেষ অবধি সব সমাজ ও রাষ্ট্রে আজ হোক আর কাল এই কট্টরপন্থা বা অন্ধত্বের পরাজয় ঘটবেই। বিজয় লাভ করবে উদারতা। আর সেই উদার রাষ্ট্র সমাজে সংস্কৃতিনির্ভর উদার জাতীয়তাবাদ অনেক বড় নিয়ামক ওই সমাজের মানুষের পথ চলার ক্ষেত্রে। সে পথ চলা হয়– গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে খাঁটি সোনাটুকু নিয়ে– নমনীয় স্বভাবে– ভবিষ্যতের দিকে। বাঙালির জন্যেও সে পথ ভবিষ্যতের গহ্বরে অপেক্ষা করছে। কারণ কোনও মানুষ নয়, মানব সমাজ ও সভ্যতাই চিরস্থায়ী। সংস্কৃতি নির্ভর জাতীয়তাবাদ কখনও কট্টর নয়। বাঙালি কোনও একদিন ঠিকই সংস্কৃতিনির্ভর জাতীয়তাবাদ বা মানববাদেরই একটি রূপ খুঁজে পাবেই। তার জন্যে কিছু দেরি হলেও কোনও ক্ষতি নেই। সভ্যতার পথে– মানব সমাজের জন্যে কয়েক’শ বছর কেন কয়েক হাজার বছরও অনেক কম সময়।
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্যে রাষ্ট্রীয় পদকপ্রাপ্ত।