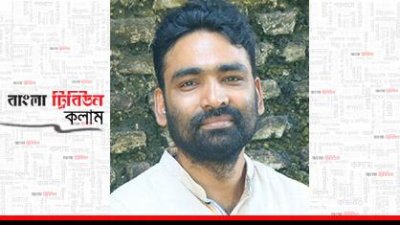আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রশ্নে আপনার মনে যেসব প্রশ্ন, আর ১০ জনের মনেও কমবেশি সেসব প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। এরকম কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে কথা বলা যাক।
১. দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে? পূর্ব ঘোষিত সময় অনুযায়ী আগামী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে? সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। বর্তমান সংসদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি। সে হিসেবে এই সংসদের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালের ৩০ জানুয়ারি। তার মানে ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারির মধ্যে যেকোনও দিন নির্বাচন করা যাবে। আরও পরিষ্কার করে বললে আগামী পয়লা নভেম্বর থেকে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে। তবে এর আগে যদি সংসদ ভেঙে যায় বা ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে সংসদ ভেঙে দেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে। যদিও সংসদ ভেঙে দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না বা সেরকম পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি।
২. রাজনীতির মাঠ বিরোধীদের দখলে চলে যাওয়ার আগে সরকার কি সেপ্টেম্বরে তফসিল ঘোষণা করে নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সেই চেষ্টা করলে কি তা সফল হবে?
৩. বিরোধীদের আন্দোলন এবং সব ধরনের বিদেশি চাপ উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ যদি সত্যিই বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন সম্পন্ন করে ফেলতে পারে, তারপর কী হবে?
৪. নির্বাচন ইস্যুতে বড় দুটি দল যদি কোনও ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে কিনা? নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়লে দেশবাসীকে তার খেসারত কীভাবে দিতে হবে?
৫. বিএনপি সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে যে আন্দোলন করছে, সেটির পরিণতি কী হবে বা তারা আন্দোলনের এই গতি কতদিন ধরে রাখতে পারবে? বিশেষ করে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবিতে বিএনপি কতদিন অনড় থাকতে পারবে? নাকি নির্বাচনকালীন সরকারের দাবি থেকে সরে গিয়ে তারা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে অন্য কোনও সমঝোতায় আসবে?
৬. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি এবং তার শরিকরা যেভাবে আন্দোলনের মাঠ গরম করার চেষ্টা করছে এবং শাসক দলও যেভাবে পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে মাঠে রয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত এই দুইপক্ষ কি বড় ধরনের সংঘাতে জড়াবে?
৭. প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সংঘাতে জড়ালে সেটির পরিণতি কী হয়, তার বড় উদাহরণ ২০০৬-০৭ সালের আন্দোলন এবং যার পরিণতি দেশে জরুরি অবস্থা জারি; অনির্বাচিত একটি সরকারের দুই বছর ক্ষমতায় থাকা; শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার, কারাগারে নির্যাতন ইত্যাদি। অতএব, এবারও যদি রাজনীতি সেই একই পথে হাঁটে, তাহলে তার প্রথম ও প্রধান ভিকটিম হবেন যে রাজনীতিবিদরাই, সেটি রাজনীতিবিদরাও জানেন। অতএব, তারা কি সেই সংঘাতের পথে হাঁটবেন বা সংঘাত উসকে দেবেন?
৮. রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হলে অনেক সময় অরাজনৈতিক গোষ্ঠী সেখান থেকে সুবিধা নিতে চায়। তারা তখন ওই ঘরপোড়ার মধ্যে আলুপোড়া খাওয়ার ধান্দায় থাকে। ফলে সেরকম কোনও গোষ্ঠী যদি রাজনীতিকে সত্যিই সংঘাতের দিতে ঠেলে দিতে উসকানি দেয়, তাহলে সেখান থেকে সচেতনভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার মতো কৌশল রাজনৈতিক দলগুলোর আছে কিনা?
৯. রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠলে কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে থাকলে সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর ভূমিকা কী হবে? সরকার কি দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?
এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। কিছু কিছু ধারণা করা যায়। যে ধারণা আপনিও করতে পারেন। তবে এর বাইরে আরও কিছু বিষয়ে নজর দেওয়া যাক।
নির্বাচনকালীন সরকার:
আগামী জাতীয় নির্বাচন প্রশ্নে মূল প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মূলত নির্বাচনকালীন সরকার প্রশ্নে। অর্থাৎ কোন সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে? ক্ষমতাসীন দল বিগত দুটি নির্বাচনের মতোই দলীয় সরকারের অধীনে, অর্থাৎ শেখ হাসিনা সরকারপ্রধান থাকা অবস্থায় নির্বাচন করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেও বিএনপি ও তার শরিকদের অবস্থান পুরোপুরি বিপরীতে। তাদের দাবি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার—যে সরকারের প্রধান থাকবেন শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কেউ। কিন্তু সংবিধান সংশোধন ছাড়া বিরোধীদের এই দাবি মানা সম্ভব কিনা, সেটিও বিরাট প্রশ্ন। তারও চেয়ে বড় প্রশ্ন, ক্ষমতাসীন দল কেন এমন একটি পদ্ধতিতে নির্বাচন দিতে রাজি হবে, যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে তাদের হেরে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে? দ্বিতীয়ত, নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার মতো সাংগঠনিক শক্তি এবং জনভিত্তি কি বিএনপির আছে?
ভোটাধিকার:
এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে বিগত দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অসন্তুষ্টি রয়েছে। কেননা, অধিকাংশ মানুষ ভোট দিতে পারেননি বা তাদের ভোট দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। অথচ সংবিধান তাকে বলেছে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক। জনগণ যে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে কেবল ভোটাধিকারের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন তার সেই ভোটের অধিকারটাই থাকে না, তখন সংবিধান প্রদত্ত মালিকানা থেকেও সে বঞ্চিত হয়। অতএব, যে মানুষ কোনোদিন কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না; যিনি কোনও দলের ডেডিকেটেড ভোটার নন—তিনিও চান এবার পছন্দের প্রার্থীকে নিজের ভোটটা দিতে। কিন্তু ভোট যদি অংশগ্রহণমূলক না হয়; যদি প্রধান দলগুলো ভোটে অংশ না নেয় এবং ভোটের পরিবেশ যদি শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ না হয়—তাহলে ওই দলনিরপেক্ষ ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে উৎসাহ পাবেন না। ফলে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জনমনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক; নির্বাচনে জয়ী হয়ে যে দলই সরকার গঠন করুক না কেন, সাধারণ মানুষ তাদের ভোটটি দিতে পারবে কিনা?
বহুদলীয় খেলা:
নির্বাচন যদি একটি রাজনৈতিক খেলা হয়, তাহলে আগামী জাতীয় নির্বাচনের খেলায় শুধু আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলই খেলোয়াড় নয়, বরং এবার বিদেশি শক্তিও মাঠে আছে। তারাও খেলছে। তাদের মধ্যেও দল-উপদল রয়েছে। এবারের নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, চীন, রাশিয়া, জাপানের মতো দেশগুলোও খেলোয়াড়। বিগত দুটি নির্বাচনে তারা ছিল দর্শক। এবার দর্শক সারি থেকে তারা মাঠে নেমেছে। অতএব, খেলার ফলাফল অনেকটা তাদের ওপরেই নির্ভর করছে। ফলে যে প্রশ্নটি জনমনে রয়েছে তা হলো, বিদেশি শক্তিগুলোর ভূমিকা এই নির্বাচনে কী হবে এবং খোদ সংসদে দাঁড়িয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যে বললেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে যেকোনও দেশের সরকার ফেলে দিতে পারে—সেই কথা তিনি কি নির্বাচনি মাঠে তাদের অংশগ্রহণ মাথায় রেখেই বলেছেন?
প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আওয়ামী লীগ থাকলো কি বিএনপি—তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কী আসে যায়? তারা কি সত্যিই গণতন্ত্র-মানবাধিকার-নাগরিকের বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে? যদি তা-ই হয় তাহলে প্রশ্ন, পৃথিবীতে আরও অসংখ্য দেশে মানবাধিকার-গণতন্ত্র-বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ—সেসব দেশেও কি যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের হস্তক্ষেপ করে? তাছাড়া পৃথিবীর কোন দেশে গণতন্ত্র আছে বা নেই, তা নিয়ে তাদের এত মাথা ব্যথা কেন? তারা কি সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রের সোল এজেন্ট? নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে বিএনপি এবং নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসেরও ভূমিকা আছে? জনমনে এই প্রশ্নও আছে।
কার অধীনে ভোট?
দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যে সম্ভব নয়, সেটি দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করে। তার পেছনে অসংখ্য কারণও রয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না এবং মাঠ প্রশাসনও যে নির্বাহী বিভাগের আদেশের বাইরে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন করতে পারে না, সেটিও বারবার প্রমাণিত। মূলত এসব কারণেই নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবি জোরালো হচ্ছে।
এরকম বাস্তবতায় বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় ‘ভোটারদের ভয়ভীতি, হয়রানি বা হামলা প্রতিরোধে’ শান্তিরক্ষী মোতায়েনের জন্য জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে চিঠি দিয়েছেন ১৪ জন কংগ্রেসম্যান। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা এএফপির বরাতে এই খবরটি দেশের একাধিক গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। এটি এই মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। অর্থাৎ যখন নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে প্রধান দুই দল বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে এবং তাদের মধ্যে সমঝোতার কোনও লক্ষণ নেই এবং যখন দলীয় ও নির্দলীয় সরকারের মাঝামাঝি কোনও সমাধানের পথ বের করা যায় কিনা এরকম আলোচনাও চলছে—তখন এই খবরের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। অর্থাৎ যদি সত্যিই নির্বাচনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা মোতায়েন থাকেন, তাহলে কি তুলনামূলক একটি ভালো ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সম্ভব?
এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন অবশ্য ভিন্ন। তা হলো, ১৭ কোটি মানুষ এবং প্রায় ১২ কোটি ভোটারের দেশে যেখানে একদিনে একসঙ্গে তিনশ’ আসনে ভোট হয়; যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ভোটকেন্দ্র থাকে এবং যে দেশে একই দিনে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়, সেই দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সর্বোচ্চ কতজন সদস্যকে মোতায়েন করা সম্ভব হবে এবং তারা সর্বোচ্চ কতগুলো আসনে কিংবা কতগুলো কেন্দ্রের ভোট পাহারা দেবেন?
এই ইস্যুতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ভোট হলে সেটি কি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এবং এই দেশের মানুষের জন্য সম্মানজনক হবে? জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের মোতায়েন করা হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সংঘাতপূর্ণ দেশে। সুতরাং বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন যদি তাদের অধীনে হতে হয়, তাহলে একটি উদীয়মান অর্থনীতির বিপুল সম্ভাবনাময় একটি দেশকে পৃথিবীর মানুষ কি আফ্রিকার সুদান বা নাইজেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ পাবে না? রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বৈরিতার কারণে বাংলাদেশের মানুষ কেন বিশ্বের কাছে হেয় হবে? তার চেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিরা নাক গলানো কিংবা ধমক দেওয়ার যে সুযোগ পাচ্ছে, তার দায় কার? ক্ষমতাসীন দল কি এই দায় এড়াতে পারে?
১৪ জন কংগ্রেসম্যানের এই চিঠিটা আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো এই চিঠিতে বলা হয়েছে, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সরকারের কথিত অপরাধের তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘের উচিত মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের সদস্যপদ অবিলম্বে স্থগিত করা। সেই সঙ্গে র্যাবের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে তাদের মোতায়েন বন্ধেরও দাবি জানানো হয়েছে। জাতিসংঘ এই চিঠি আমলে নেবে কিনা বা এই চিঠির আলোকে সত্যিই কোনও ব্যবস্থা নেবে কিনা সেটি সময়ই বলে দেবে। কিন্তু এই ধরনের চিঠি দেওয়ার মতো যে পরিস্থিতি তৈরি হলো, সেটি খুব ভালো কথা নয়। অতএব, জনমনে এই প্রশ্নও আছে বিদেশিরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর সাহস পাচ্ছে কোথায়? কাদের কর্মকাণ্ডের কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো?
লেখক: কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, নেক্সাস টেলিভিশন।