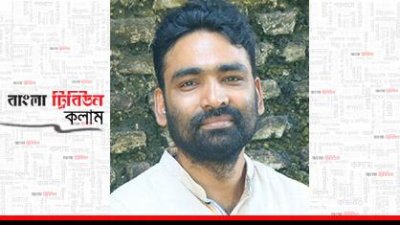যেকোনও অঙ্কের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে; যার মধ্যে থাকে গ্যাস-বিদ্যুৎ-জ্বালানি তেলে ভর্তুকি কমানো। ভর্তুকি কমানো মানে দাম বাড়ানো। শুধু তাই নয়, কৃষি খাত এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতেও তারা ভর্তুকি কমাতে বলে।
সবশেষ বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ-এর প্রতিনিধিরা যখন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বৈঠক করলেন, সেখানেও তারা নানা খাতে ভর্তুকি কমানোর পরামর্শ (শর্ত) দিয়েছেন।
কিন্তু জনমনে এই প্রশ্নও আছে যে, আইএমএফ ঋণ দেবে, নিয়মিত কিস্তি নেবে। কিন্তু তারা কেন বারবার বিদ্যুৎ জ্বালানি, কৃষি এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ভর্তুকি কমানোর শর্ত বা চাপ দেয়? তারা সময়মতো কিস্তি পেলেই তো হয়। বাংলাদেশ কোথায় কতটুকু ভর্তুকি দেবে, এটি নিয়ে তাদের মাথাব্যথা কেন? অর্থাৎ সরকার যদি ভর্তুকি দিয়ে তাদের কিস্তি চালাতে পারে, সেখানে আইএমএফ-এর সমস্যা কোথায়?
প্রশ্নটা অন্যভাবেও করা যায় যে, বাংলাদেশ কেনই বা এসব শর্ত মেনে ঋণ নেয়? কেননা আইএমএফ জোর করে কাউকে ঋণ দেয় না। অর্থাৎ আইএমএফ-এর কাছ থেকে ঋণ না নিলে বাংলাদেশের কি খুব বেশি ক্ষতি হবে? তাছাড়া তাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সব জায়গায় ভর্তুকি কমানো হলে দেশে অস্থিরতা তৈরির শঙ্কা আছে। অসংখ্য মানুষ সঞ্চয়পত্রের মুনাফার ওপর নির্ভরশীল। আইএমএফ সেখানেও ভর্তুকি কমাতে বলে। তারা আসলে কী বলতে চায় বা কী করতে চায়, সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আর আমাদেরও ভাবা দরকার, এদের কাছ থেকে ঋণ না নিলে আমরা খুব বেশি অসুবিধায় পড়বো কিনা?
অনেকে মনে করেন, আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো চায় বাংলাদেশের মতো দেশগুলো ঋণনির্ভর থাকুক। ঋণের দুষ্টুচক্রে তারা আটকে যাক—যাতে দেশগুলো ওইসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে পারে। ঋণনির্ভর রাষ্ট্রগুলোয় অস্থিরতা ও সংকট জিইয়ে রাখা গেলে বিশ্বব্যাংক আরইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো যারা চালায়, সেই ধনী রাষ্ট্রগুলোর খবরদারি করা সহজ হয়। তারা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন ইত্যাদি ইস্যুতে ওইসব দেশকে চাপে রাখার বিনিময়ে নিজের ভূরাজনৈতিক স্বার্থ ও তাদের দেশীয় কোম্পানির ব্যবসার দরজাটা খোলা রাখতে চায়। অর্থাৎ দিন শেষে সবই ব্যবসা ও টাকার খেলা। বৈশ্বিক রাজনীতির খেলা। অতএব বৈদেশিক ঋণও সেই বৈশ্বিক রাজনীতির বাইরের কিছু নয়।
জনমনে এ প্রশ্নও আছে যে, বাংলাদেশকে তারা যে চাপ বা শর্ত দেয়, ঋণের কিস্তি পাওয়ার শর্ত হিসেবে তারা কি অন্য সব দেশকেও একই শর্ত দেয়? সিনিয়র সাংবাদিক সেলিম খান লিখেছেন, ‘আর্জেন্টিনা বা সুরিনামকে যে চাপ সহ্য করতে হচ্ছে, সেই একই চাপ নিতে হচ্ছে না মিসর বা পাকিস্তানকে। কারণ দেশ দুটি দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার ‘কৌশলগত’ বন্ধু। যেমন, আইএমএফের শর্ত হিসেবে পাকিস্তানের সেলস ট্যাক্স বা বিক্রয় কর ব্যবস্থার সংস্কারের কাজ ঝুলে আছে সেই ১৯৯৭ সাল থেকে। কিন্তু তাতে দেশটির আইএমএফের সাথে ঋণ নিয়ে আলোচনায় বিশেষ কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।’
প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ)-এর হিসাবে, বর্তমানে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার কাছে বাংলাদেশের ঋণ প্রায় ৭ লাখ ৫৯ হাজার কোটি টাকা। এই হিসাব ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত। আইএমএফও মনে করে, বাংলাদেশের ঋণ এখনও ঝুঁকি সীমার মধ্যেই রয়েছে। বলা হয়, জিডিপির ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণের স্থিতি যেকোনও দেশের জন্য নিরাপদ। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ জিডিপির সাড়ে ১৫ শতাংশের নিচে।
আশার সংবাদ হলো, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ঋণখেলাপি হয়নি। গত বছরের ৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন, বাংলাদেশ ঋণ পরিশোধে কখনও খেলাপি (ডিফল্টার) হয়নি, হবেও না। দেশের অর্থনীতির ভিত্তি অনেক মজবুত, সরকার অত্যন্ত সতর্ক। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে এখন পর্যন্ত উন্নয়নে যত ঋণ নিয়েছে, সব ঋণ সময়মতো পরিশোধ করা হয়েছে। (প্রথম আলো, ০৬ এপ্রিল ২০২২)।
সুতরাং যে দেশের ঋণখেলাপি হওয়ার রেকর্ড নেই এবং যে আইএমএফও বলছে যে, বাংলাদেশের ঋণ এখনও ঝুঁকি সীমার মধ্যেই রয়েছে—সেই দেশকে ঋণ দিতে গিয়ে তারা কেন এমন সব শর্ত দেয়, যেগুলো মানতে গেলে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চাপ বাড়বে?
বিদ্যুৎ-জ্বালানি-কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ভর্তুকি কমানোর মানে হলো উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়া। আইএমএফ যেসব শর্ত দিয়েছে, সেগুলো মানতে গেলে সরকারকে অনেকগুলো অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম এমনিতেই কয়েক দফা বেড়েছে। জিনিসপত্রের দাম নিয়েও মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আছে। এমতাবস্থায় নতুন করে ভর্তুকি কমানো মানে সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবার দাম বৃদ্ধি। ফলে এ মুহূর্তে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া সরকারের জন্য বেশ কঠিন। তার চেয়ে বড় কথা বা বড় প্রশ্ন হলো, আইএমএফ যদি সময়মতো তাদের কিস্তির টাকা পায়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোথায় কী পরিমাণ ভর্তুকি দিলো—সেটি নিয়ে তাদের আপত্তি বা সমস্যা কোথায়?
এটা ঠিক যে, বাংলাদেশের ওপর বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ১০৫ কোটি ডলার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। ছয় মাসে এত ঋণ পরিশোধ আগে কখনও করা হয়নি। সামনে আরও বেশি ঋণ পরিশোধ করতে হবে এমন পূর্বাভাসও আছে।
চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সব মিলিয়ে ২৭৮ কোটি ডলার পরিশোধ করতে হবে। প্রতিবছরই এ পরিমাণ বাড়বে। (প্রথম আলো, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)। অতএব যেকোনও অঙ্কের ঋণ নেওয়ার আগে বাংলাদেশকে ভাবতে হবে, সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা তার আছে কিনা। আর যেহেতু বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নিতে গেলে কিছু শর্ত মানতেই হয়, ফলে সেখানেও বাংলাদেশকে এই বিবেচনাটি রাখতে হয় যে, সব শর্ত পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব কিনা?
অস্বীকার করার উপায় নেই, বেশ কিছু খাতে সরকারের ভর্তুকি নিয়ে প্রশ্ন আছে, বিশেষ করে যেসব ভর্তুকি সাধারণ মানুষের কোনও কাজে লাগে না। যেমন, রাষ্ট্রায়ত্ত যেসব প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর লোকসান গুনছে, অথচ যাদের লাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়ার কথা, যেমন– বাংলাদেশ বিমান, রেল, রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন করপোরেশন। যেগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিলে লোকসান নয়, বরং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, সেসব প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর ভর্তুকি দিতে হবে কেন– তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ তো বটেই, সাধারণ মানুষের মনেও প্রশ্ন আছে। লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে ভর্তুকি বন্ধ হয়ে যাবে; তখন জবাবদিহি বাড়বে বলে ইচ্ছা করেই সেগুলোকে অনেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে দেন না– এই নির্মম সত্যও এখন আর গোপন নয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলোয় ভর্তুকি বন্ধ করে সেগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া কিংবা লাভজনক করার জন্য পদ্ধতি গড়ে তোলার বিকল্প নেই।
যেসব শর্ত মানলে বিদ্যুৎ-জ্বালানি-কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ভর্তুকি কমাতে হবে, তার বাইরেও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য আইএমএফ বা বিশ্ব ব্যাংক কিছু শর্ত আরোপ করে। অর্থাৎ অর্থ খরচে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করার যে তাগিদ দেওয়া হয়, সেইসব শর্ত বাংলাদেশ কতটুকু পূরণ করতে পারছে, সেই প্রশ্নটি নিজেদেরই করা উচিত।
প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমন করে পুরো রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার পথ যে এখনও বন্ধুর, সেটি অস্বীকারের সুযোগ নেই। সুতরাং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কী বললো, কী শর্ত দিলো, তারা ঋণ দিলো কি দিলো না—তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, বাংলাদেশ নিজে কী করছে? সুশাসনের পথে তার অর্জন কতটা সন্তোষজনক। জনকর্মচারীরা কতটা জনবান্ধব। জনগণের অর্থ খরচের জায়গাটি কতটা স্বচ্ছ। উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের কত শতাংশ খরচ হয় আর কত শতাংশ দুর্নীতির শিকার হচ্ছে—সেই প্রশ্ন বাংলাদেশের নাগরিকদের মনেই আছে। বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এসব প্রশ্ন করুক বা না করুক, বাংলাদেশের জনগণকেই প্রশ্নগুলো জারি রাখতে হবে।
লেখক: কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর, নেক্সাস টেলিভিশন।
*** প্রকাশিত মতামত লেখকের একান্তই নিজস্ব।